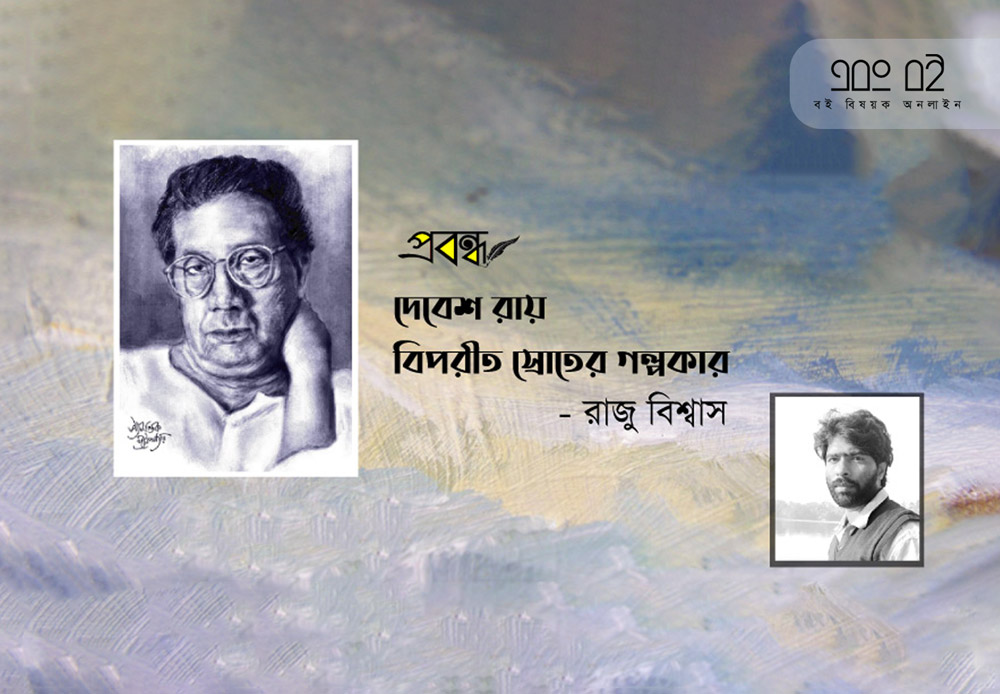লেখক কমলকুমার মজুমদার সম্পর্কে বলতে গিয়ে “কথাসাহিত্যের নতুন সংজ্ঞা” প্রবন্ধে দেবেশ রায় লিখেছিলেন : “অনুভূতির ও অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ, ভাষার বহন ও ধারণ ও ধারণক্ষমতাবৃদ্ধি, বিষয়ের পরিধিপ্রসার-তাঁর রচনামাধ্যমে এই কাজগুলি বা এর কোনও একটিও করে ওঠা একজন কথাশিল্পীর সার্থকতার অনস্বীকার্য চিহ্ন।”
বস্তুত বাংলা কথা সাহিত্যের প্রয়াত কিংবদন্তি কথাকার দেবেশ রায় তাঁর রচনায় এই কাজগুলি যথাযথভাবে করে উঠতে পেরেছেন। উপন্যাসের জগতে তিনি যেমন ব্যতিক্রমী পথযাত্রী, তেমনি ছোট গল্পের মাটিতেও তাঁর স্বতন্ত্র পদচারনা। এ কথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না বাংলা কথাসাহিত্যে কমলকুমার মজুমদারের মানস উত্তরসূরি দেবেশ রায়। তবে কমলকুমার তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে খুব অল্পই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু দেবেশ রায়ের সৃষ্টিসম্ভার বিপুল। মহাকাব্যিক উপন্যাস “তিস্তাপারের বৃত্তান্ত” তাঁকে প্রভূত খ্যাতি এনে দিয়েছে। বাংলা ছোটগল্পের বিষয় ও আঙ্গিক নিয়েও তাঁর নিরন্তর পরীক্ষানিরীক্ষা সমালোচক ও মেধাবী পাঠককে বিস্মিত করে। উপন্যাস বাদেও একজন ব্যতিক্রমী গল্পকার হিসেবেও তাঁর অবস্থান আন্তর্জাতিক স্তরের। সস্তার পাঠকপ্রিয়তা তিনি চাননি। কমলকুমারের মতই দীক্ষিত পাঠকের লেখক দেবেশ রায়। তাঁর গল্পভাষা একেবারেই তাঁর নিজস্ব।
১৯৩৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশের পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামে দেবেশ রায়ের জন্ম। দেশভাগের আগে ১৯৪৩ সালে তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি চলে যান। দীর্ঘকাল উত্তরবঙ্গবাসের অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেয় তাঁর অসামান্য উপন্যাস “তিস্তাপারের বৃত্তান্ত”। উপন্যাসটির জন্য ১৯৯০ সালে ভারত সরকার তাঁকে “সাহিত্য অকাদেমি” পুরুস্কারে সম্মানিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন সাহিত্যিক দেবেশ রায়। সেই সূত্রেই গভীর যোগাযোগ স্থাপিত হয় উত্তরবঙ্গের প্রান্তবাসী মানুষের সঙ্গে। শিখে নিয়েছিলেন রাজবংশী ভাষা। কলকাতায় আসার পর তিনি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়েছিলেন ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে। শ্রমিকদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাঁর।
১৯৭৯ সাল থেকে প্রায় দশ বছর তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন ‘পরিচয়’ পত্রিকা। দেবেশ রায়ের প্রথম গল্প সংকলন ‘আহ্নিক গতি ও মাঝখানের দরজা’, ‘দুপুর’, ‘পা’, ‘কলকাতা ও গোপাল’, ‘পশ্চাৎভূমি’, ‘ইচ্ছামতী’, ‘নিরস্ত্রীকরণ কেন’, ও ‘উদ্বাস্তু’ এই আটটি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয়। পঞ্চাশের দশক থেকে লিখতে শুরু করেছেন। তাঁর প্রথম দিকের গল্পে ফর্মের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য থাকলেও তা খুব বেশি অপরিচিত ছিল না বাংলা গল্পের পাঠকের কাছে। কিন্তু সত্তর আশির দশকের লেখা গল্পে ফর্ম আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, ফর্ম ও গল্পের বিষয় একাকার হয়ে যায়। ফলত উপন্যাসের মত তাঁর গল্প সেভাবে সমাদর পায়নি সাধারণ পাঠকের কাছে।
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা হুমায়ূন আহমেদের মত ঝরঝরে গদ্যে তিনি কখনোই লেখেননি। বরং ক্রমশ তিনি গল্পবিষয় ও ভাষায় অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছেন। সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতির প্রসঙ্গ তাঁর গল্পে যেভাবে এসেছে সমকালীন আর কারো গল্পে তেমনটা দেখা যায় না। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন এই জটিলতা তাঁকে সাধারণ পাঠকের থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। সাধারণ পাঠক গল্পে আখ্যান চায়। চায় বিনোদন। কিন্তু তথাকথিত চিত্ত বিনোদনের জন্য লেখক হিসেবে তিনি দায়বদ্ধ নন। তাঁর দায়বদ্ধতা বৃহত্তর সময় ও সমাজের কাছে।
লেখক হিসেবে কমলকুমার মজুমদারের মত দুরূহ পথটিকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। এবং সাফল্যের সঙ্গে আজীবন সে পথেই হেঁটেছেন। তবে জীবনের শেষ পর্বে তিনি অপেক্ষাকৃত সরল আখ্যানধর্মী গল্পের পথে ফিরে এসেছিলেন অনেকটাই।পাঠক উপন্যাসিক দেবেশ রায়কে যেভাবে গ্রহণ করেছে, ছোটগল্পকার দেবেশ রায়কে সেভাবে পারেনি। খুব অল্প সংখ্যক গল্প যেখানে তাঁর ভাষাভঙ্গি অপেক্ষাকৃত সরল, বিষয়ের মধ্যে আছে ঐতিহ্যবাহী পরিচিত সরস মালমসলা তেমন কিছু গল্পকেই পাঠক বেশি করে গ্রহণ করেছে। সেগুলির মধ্যেই কয়েকটি গল্প আলোচনার মাধ্যমে দেবেশ রায়ের গল্পকার সত্তার সামান্য পরিচয় এখানে নেওয়া যেতে পারে।
দেবেশ রায়ের ‘আহ্নিকগতি ও মাঝখানের দরজা’ অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গল্প। এ গল্পে লেখক তিনটি চরিত্রের পারস্পারিক সম্পর্ক ও তাকে ঘিরে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও জটিলতার এক আশ্চর্য আবহ নির্মাণ করেছেন। গল্পের আখ্যানভাগটি পাঠকের খুব চেনা। কিন্তু অচেনা বিষয়টি হল লেখকের অনবদ্য উপস্থাপন কৌশল, বর্ণনা ও ভাষাভঙ্গি।
শিশিরের দাদা প্যারালিসিস আক্রান্ত। দীর্ঘদিন সে ঘরবন্দি। স্ত্রী তটিনী তার সন্তানদেরকে যেমন স্নান করিয়ে দেয়, তেমনিভাবে নিজের স্বামীকেও। শিশিরের দাদার কোনও নাম দেননি লেখক। সে যেন একটা শিশুর মতই তটিনীর সংসারে প্রতিপালিত। দাদা উপার্জনহীন। সংসারের অভাব পূরণ করতে অফিসের পর বাড়তি ট্যুইশন করে অনেক রাতে বাড়ি ফিরতে হয় শিশিরকে। তটিনী শিশিরের জন্য সিগারেট আর সুপারি তৈরি রাখে। বৌদি শিশিরকে সিগারেটের রুটিন তৈরি করে দেয়। দিনে পাঁচটা। কিন্তু রাতে খাওয়ার পর সে কথা রাখতে পারে না শিশির। প্যাকেট থেকে বাড়তি সিগারেট টেনে নিতে গেলে “খপ করে হাত থেকে সেটা কেড়ে নেয় তটিনী।’
আসলে গল্পকার শিশির আর তটিনীর পারস্পারিক সম্পর্কের পালাবদলকেই বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে চিহ্নিত করে তুলতে চান। অনিবার্যভাবে শিশির আর তটিনী পরস্পরের নিবিড় সান্নিধ্যে আসে, কিন্তু আশ্চর্য দক্ষতায় লেখক বারবার তাদের আসন্ন অনিবার্য জৈবনিক সম্পর্কের ইঙ্গিতকে আড়াল করেন। দীর্ঘদিন স্বামী সোহাগ বঞ্চিত তটিনী ‘ঠাকুরপো’ শিশিরের কাছে তার অক্ষম দাদার গল্প শোনায়। সারাদিন জড়ভরত হয়ে বসে থাকলেও রাত্রে তার দাদা তটিনীকে কাছে পেতে চায়। পঙ্গু মানুষটা তার অক্ষম যৌবনের তীব্র আক্রোশ নিয়ে যেন তটিনীকে গ্রাস করতে চায়। কিন্তু সে কদর্য বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে তটিনী সমবয়সী দেওর শিশিরের কাছে ছুটে আসে। কিন্তু আগুনটা জ্বলতে জ্বলতেও জলে না।
দাদার ঘর আর শিশিরের ঘরের মাঝখানে একটা দরজা। সেটা সারাদিন খোলাই থাকে। কেবল রাত হলে বন্ধ হয়ে যায়। এই মাঝখানের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে তটিনী প্রতিদিন একটা পেন্ডুলামের মত দোল খায়। আহ্নিকগতির মত বয়ে চলে জীবন : “জীবনটা গড়ায়। এক সকাল, এক রাত। একই কাজ, কাজ। অলস বিশ্রাম। রাত্রি। তটিনী দরজা বন্ধ করে। দরজায় তীব্র ধাতব আওয়াজ ওঠে। …জীবনটা একটা ভাঙা রেকর্ড, বাজতে বাজতে সেই ভাঙায় ঠেকে একই আওয়াজ। …জীবন বিধাতা এক-গত-শেখা সারেঙ্গিওয়ালা। সকালে দুপুরে রাত্রে দিন মাস বছরে সেই একই গত বেজে চলে, …মাঝে মাঝে তার ছেঁড়ে। কিন্তু সেটা তো জীবন নয়, জীবনের পাদটীকা।”
কিন্তু ‘জীবনের পাদটীকা’ হলেও সারেঙ্গিওয়ালার ছেঁড়া তারে আবার যে নতুন তারের সুর ওঠে তাতে শিশিরের দাদার সন্তান খোকন বিল্টুর মাঝখানে আসে আরও একটি সন্তান। খোকন জেনে যায় ‘পিতা’ আর ‘জনক’ শব্দের পার্থক্য। কেটে যায় বেশ কতকগুলো বছর। জীবন চলে তার নিজস্ব নিয়মে। কিন্তু মাঝখানের দরজাটা চিরকালের মত খোলা রইল। অবিবাহিত শিশিরের ঘরে আর নতুন বউ আসে না। খোকনের মা আর শিশির কিন্তু এখনো অপেক্ষা করে আবার কবে সারেঙ্গিওয়ালার তার ছিঁড়বে…।
ভাষার ব্যঞ্জনা যে কত গভীর হতে পারে দেবেশ রায় বহু লেখায় তা দেখিয়েছেন। কোনও লেখকই আকাশ থেকে পড়েন না। তাকে ঐতিহ্যের পথ ধরেই আসতে হয়। দেবেশ রায়ের প্রথম দিকের গল্পে যেটুকু আখ্যানের ছিটেফোঁটা ছিল, পরবর্তীকালের গল্পে একেবারেই তা দেখা যায় না। দেবেশ রায়ের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ কিছুটা আলব্যের ক্যামুর সমধর্মী। ‘আউট সাইডার’ এ নায়ক মোরেসের পার্সপেক্টিভ থেকে আমরা যে ভাবে অনুভব করতে পারি ভিন্ন এক বাস্তবতাকে; সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধের বিপরীতে গিয়ে নায়ক মোরেস যেভাবে প্রমাণ করে দেয় আমাদের চেনা জানা সত্যের ভিতরেও অপর এক সত্যের অস্তিত্ব আছে; তেমনভাবেই দেবেশ রায় তাঁর গল্পে মনলোকে আলো ফেলে চরিত্রের গহন থেকে তুলে আনেন পরিপূর্ণ ব্যতিক্রমী এক জীবনবোধকে। প্রচলিত বাস্তববাদী সাহিত্য রচনার গত থেকে সরে এসে তিনি যে কাহিনি আমাদের শোনান তা এক দিকে যেমন পাঠকের ভাবনাকে শাণিত করে, অপর দিকে নতুন এক অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়।
দেবেশ রায়ের ‘দুপুর’ গল্পটি একটি নিখুঁত মনস্তাত্ত্বিক গল্প; যেখানে একটি দুপুরের চিত্রকল্পকে আশ্রয় করে লেখক পৌঁছে যান পাঁচটি অসমবয়সী চরিত্রের মনোজগতের গহনে। অসাধারণ কাব্যিক ও ব্যঞ্জনাময় ভাষায় গল্পকার জ্যৈষ্ঠ মাসের এক রোদজ্বলা দুপুরকে পাঁচটি চরিত্রের পার্সপেক্টিভ থেকে আলাদা আলাদাভাবে চিত্রিত করেছেন। অনেকটাই কুরোসওয়ার ‘রশোমন’ ছবির সেই বিখ্যাত হত্যাদৃশ্যের মত।

নিম্ন মধ্যবিত্ত চল্লিশ পেরনো যতীনবাবুর পরিবারে তিন সন্তান- চোদ্দ বছরের ছোট মেয়ে সতী, বছর আঠেরোর ছেলে মুকুল, বড় মেয়ে বছর কুড়ির মায়া ও পঁয়ত্রিশ পেরনো স্ত্রী রেণুবালা। সপ্তার অন্যদিনগুলো কাজের মধ্যে কেটে গেলেও একমাত্র রবিবার যতীনবাবুর পরিবারে একটুখানি অবসর বিনোদনের দিন। এদিনই পরিবারের কর্তার জন্য বরাদ্দ থাকে একটি ডাব ও দুটো পান। এই ডাব ও পানের অত্যল্প বিলাসিতাটুকু ছাড়া এই পরিবারে আর সামান্য কোনও বিলাসিতার অবকাশ নেই। প্রাত্যহিকতার পীড়নে ধ্বস্ত অকাল-পড়ন্ত যৌবনা রেণুবালার কাছে দুপুরটা তাই “ছোট্টখাটো ভুঁড়িঅলা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোকের মত”। সে অনুভব করে : “দুপুরের শরীরের শক্তিটা চর্বি হয়ে যাচ্ছে, চর্বিটা হাড়টাকে ঢেকে দিচ্ছে, হাড়ের স্পর্শ আর পাওয়া যায় না, মোটা থলথলে ভুঁড়ি যেন গায়ের সঙ্গে লাগে আর পিছলোয়।”
দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সকলেই শুয়েছে। কিন্তু কেউই ঘুমায়নি। সকলেই ভাবছে সে ছাড়া অন্যরা ঘুমাচ্ছে। রেণুবালার সাধ হয় আবার মাতৃত্বের স্বাদ পেতে। দুপুরের পেটের ভিতর সে একটা বাচ্চার নড়াচড়া অনুভব করে। যতীনবাবুর মনে হয়, “অনেক ছেলের মা, শিথিল দেহ, শ্লথযৌবন নারীর মত দুপুরটা হাঁপসাচ্ছে।” এমনই রঙহীন দুপুরের অনেক উপমা তার ভাবনায় আসে। সকলেই দুপুরের মধ্যে এক বেহালার অস্ফুট সুর শুনতে পায়। কিন্তু কেউই সুরটাকে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি শুনে উঠতে পারে না। মায়া তার সদ্য যৌবনের অস্ফুট বাসনা নিয়ে দুপুরটাকে “ফটোয় দেখা পুরুষকে কল্পনা করার মতই বাস্তব অথচ অলীক” দ্যাখে। কিশোরী সতীর কাছে দুপুরটা ভীষণই রঙিন। তার কাছে : “টইটম্বুর, টসটস করছে দুপুরটা। মধ্য সমুদ্রের মত নিস্তরঙ্গ, বিরাট,ব্যাপক; চুম্বক পাহাড়ের মত আকর্ষক; ফুলশয্যার পুরুষের মত স্থির, সবল, জ্বলন্ত।”
কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলেই অতৃপ্ত রয়ে যায়। কারো কাছেই দুপুরটা পুরোপুরিভাবে ধরা দেয় না। যে অলীক বেহালাটার সুর এক রহস্যলোকের সৃষ্টি করেছিল, এক মায়াবী স্বপ্নঘোর তৈরি করেছিল অচিরেই তা “একটা ট্রাকের জান্তব আওয়াজে” ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। দুপুরটা গড়িয়ে যায় বিকেলের দিকে। পরিবারের পাঁচজন সদস্যই পরস্পরের মুখের দিকে অনন্তকাল ধরে যেন কিছুর প্রত্যাশায় চেয়ে থাকে। এ গল্পের শেষে পাঠক অদ্ভুত এক অনুভূতির মুখোমুখি হন। এক অস্ফুট বিষণ্ণতা তাকে গ্রাস করে। দুপুরের চিত্রকল্পগুলির সঙ্গে চরিত্রের মনোলোকের তীব্র অন্বয় এক অনাঘ্রাত বোধের জন্ম দেয়। এভাবে একটি দুপুরকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত করে দেবেশ রায় অসাধারণ দক্ষতায় বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহ্যশালী ধারায় নতুন এক পরিসর নির্মাণে সক্ষম হন।
আশি-নব্বইয়ের দশকে লেখা দেবেশ রায়ের গল্পগুলিতে প্রবলভাবে রাজনীতি সচেতনতার ছাপ পাওয়া যায়। এ সময় গল্পের ফর্মকে ভেঙেচুরে এক ভিন্নধর্মী গল্প আঙ্গিক নির্মাণ করতে চাইলেন তিনি। গল্পের ভিতর আসলে কোনও গল্প থাকে না, থাকে কিছু বিচ্ছিন্ন দৃশ্যকল্প; যেগুলিকে লেখক একটি অদৃশ্য সুতোয় এক বিশেষ ক্রমানুযায়ী গেঁথে দেন। পাঠকের চিন্তাজালকে বারবার ছিন্ন করে দেন লেখক; আবার নতুন করে বুনে তোলেন গল্পের এক অচেনা অবয়ব।
২০০১ সালে প্রকাশিত ‘স্বনির্বাচিত বারো’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ‘বুদ্ধ আর বুদ্ধ’ গল্পটিতে সমকালীন অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের ‘পোখরান পরমাণু বিস্ফোরণ’ এর ঘটনার প্রভাব পড়েছে। পৃথিবীতে বহুবার মানব সভ্যতার উপর নেমে এসেছে হিংসা আর ধ্বংসের করাল ছায়া। হিরোসিমা-নাগাসাকিতে পরমাণু বিস্ফোরণের পর রাতারাতি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল দুটি শহর। পরবর্তী কয়েক দশক ধরেও জাপানিরা সেই পারমাণবিক শক্তির ভয়ংকর অভিশাপের নিদারুণ আঘাত সহ্য করেছে; তবু পৃথিবীর দেশগুলো নিজেদেরকে আরও শক্তিধর করে তোলার উদ্দেশে নানা রকম হন্তারক অস্ত্রশস্ত্রের উদ্ভব করে চলেছে। চলছে পারস্পারিক ক্ষমতা প্রদর্শন। আলোচ্য গল্পে খুব স্বল্প পরিসরের মধ্যে লেখক গৌতম বুদ্ধের অহিংসতার আদর্শের বিপ্রতীপে মানব সভ্যতার এইসব ভয়ংকর হিংসাত্মক কার্যকলাপকে তীব্র ব্যঙ্গাত্মক ও তির্যক ভাষায় আক্রমণ করেছেন। গল্পের শুরুতে কথক জানিয়েছে প্রসিদ্ধ কিছু বৌদ্ধমূর্তি দর্শন, কিছু বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদির বাইরে গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে তার সম্পর্ক বা জ্ঞান বেশি নয়। বুদ্ধদেবের অহিংসার আদর্শের সঙ্গে সমকালীন পৃথিবীর অনিবার্য সংঘাত চলছে। খবরের কাগজে ফলাও করে বেরুচ্ছে রোজ এইসব খবর। মানুষ যেন বুদ্ধের সঙ্গে তীব্র রসিকতায় করছে :
“ভারত সরকার পোখরানে যে দু-দফা আণবিক বোমা ফাটালেন সেই কর্মসূচীর নাম নাকী ছিল ‘বুদ্ধের হাসি’,…এত কিছু থাকতে বোমার সঙ্গে বুদ্ধকে জড়িয়ে দেবার মধ্যে গোপন কোনও চিন্তা ধরা পড়ে যায়।…ইতিহাস তো এমন সব কাণ্ডতে ঠাঁসা। হিরোসিমার উপর পৃথিবীর প্রথম ও এখনো পর্যন্ত শেষ, আণবিক বোমাটির নাম দেয়া হয়েছিল ‘লিটল বয়, বাচ্চা ছেলে।”
বস্তুত সাধারণ মানুষের পক্ষে এই চরম বিপ্রতীপতাকে মেলানো অসম্ভব। কথকের স্ত্রী গান গেয়ে যে বুদ্ধমূর্তি উপহার পায় তার স্থান হয় ফ্ল্যাটের সবচেয়ে অন্ধকার কোনটিতে। কিন্তু কথক অনুভব করে শেষ রাত্রে সেই অন্ধকার জায়গা থেকে উজ্জ্বল বিভা ছড়িয়ে “বুদ্ধ তার ত্রিঠামে দাঁড়িয়ে আছেন।’” কিন্তু গল্পের শেষে যে আলোর উৎসারের দিকে লেখক ইঙ্গিত করেছেন তাও মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যায়। এক আশাহীন উত্তরণহীন পৃথিবী নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে :
“বড় জোড় পাঁচ পা হেঁটে বুদ্ধের সামনে পৌঁছবার আগেই, ঐ পাঁচ পা ব্যবধানের মাঝখানেই সহস্র সূর্যের আলোতে অন্ধ করে এই ফ্ল্যাটে একটা বোমা ফাটল।”২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘কালি ও কলম’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘দরজা’ গল্পটি দেবেশ রায়ের জীবন সায়াহ্নের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। জীবনের অন্তিম পর্বে এসেও লেখকের সমাজবীক্ষা যে কতটা গভীর ও তীব্র এ গল্পে তার পরিচয় আছে। সমকালীন সময়ের হৃৎস্পন্দনকে তিনি আজীবন একজন প্রাজ্ঞ দার্শনিকের মত মাপতে সক্ষম ছিলেন। ‘দরজা’ গল্পে উঠে এসেছে। অনতি অতীতে রাজ্যে যে ভুয়ো ডাক্তার আটক অভিযান চলেছে ও তার ফলে হাজার হাজার ভেকধারী, মিথ্যে ডিগ্রীধারী ডাক্তারের সন্ধান মিলেছে। মুমূর্ষু মানুষের জীবন নিয়ে এই ভঙ্ককর ব্যবসা যারা করছেন তারা হয়তো আয়নার সামনে কোনোদিন দাঁড়াবার অবসর পান না। কিন্তু সময় তাদেরকে ঠিকই চিহ্নিত করে দেয়। এ গল্পের নায়িকা অম্বিতা তার ডাক্তার স্বামীর ক্লিনিক থেকে একটা ফোন পায়। তার স্বামীকে কারা যেন ধরে নিয়ে যাচ্ছে। অম্বিতা প্রথমে ব্যাপারটাকে ততটা সিরিয়াসলি না নিলেও ক্রমশ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে :
“বিপন্নতা বোধ, আক্রান্ত হওয়ার আতঙ্ক, বাড়ির লোকের বাড়ি না ফেরার ভয়, মেয়ের ধর্ষিত হওয়ার ঘটনা- এমনই ছড়িয়ে পড়েছে হাওয়ায়, মাটিতে, ঘুমে…।”গল্পকার অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষায় অম্বিতার মনের সেই অসহার আর উদ্বেগপূর্ণ অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। তার ডাক্তার স্বামীকে কারা ধরে নিয়ে যেতে পারে। গাড়ি বের করে বাইরে বেরোনোর আগে সে টিভিতে দেখতে পায় তার স্বামী ডক্টর অনুপম গুহনিয়োগীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এই প্রথম অম্বিতা জানতে পারে তার স্বামী আসলে কোনও ডাক্তারই নয়। তার সব ডাক্তারি সার্টিফিকেট মিথ্যে। এতো ধন-ঐশ্বর্য, সম্মান আর প্রতিপত্তির নেপথ্যে আছে তার স্বামীর ঘৃণ্য প্রতারক রূপ। কেবল অম্বিতাকেই সে ঠকায়নি, সমগ্র সমাজের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। যে ডাক্তার স্বামীকে নিয়ে তার গর্ব ছিল, অহংকার ছিল তা নিমেষে লুপ্ত হয়ে যায়। লালবাজার থানায় গিয়ে অম্বিতা যে দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢোকে তাকে লেখক সাংকেতিকভাবে উপস্থাপিত করেছেন। যেন একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ পেরিয়ে অম্বিতা গিয়ে পৌঁছয় স্বামীর মুখোমুখি। দুজনের কথোপকথনের মধ্যে ডাক্তারের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুর শোনা যায় :
“ছ-বছর বিলেতে থাকা পাত্রকে তোমাদের বাড়ির লোকেরা যদি এম-আর-সি-পি ধরে নেয়, তার জন্য আমি কী দায়ী?”গল্পের শেষে উকিল অম্বিকার কাছে জানতে চেয়েছে তার সঙ্গে তার স্বামীর কতদিন বিয়ে হয়েছে। এর উত্তরে অম্বিতা জানায় সে মামলার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। অম্বিতা ঘুরে দাঁড়িয়ে সবাইকে পিছনে ফেলে বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে যায়। আসলে দরজাটা অম্বিকার জন্য আদৌ খুলবে কি না তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। এতো দিন যে সে আসলে একটা ভুয়ো ডাক্তারের সংসারে থেকে যাবতীয় সুখ-ঐশ্বর্য ভোগ করছে তার দায়কে সে অস্বীকার করবে কেমন করে? রত্নাকরের পাপের ভাগ তাকেও তো নিতে হবে।
জীবনের নানা পর্বে দেবেশ রায়ের ছোটগল্পে একাধিক পরিবর্তন এসেছে। তবে গল্প বলার রীতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার ধারা থেকে তিনি কখনোই পুরোপুরি সরে আসেন নি। অস্বীকার করেননি সমকালীন সমাজ ইতিহাসের প্রভাবকে। দেবেশ রায়ের গল্পে যৌনতা রাজনীতি সমাজ দর্শন আন্তর্জাতিকতা এ সবই পরস্পর এমনভাবে মিশে আছে যে গল্পকে কোনও বিশেষ শ্রেণিভুক্ত করা কঠিন। বলার অনেক কথা থাকলেও স্বল্পায়তন এই নিবন্ধে তা সম্ভব নয়। আরও বহু উল্লেখযোগ্য গল্প নিয়ে হয়তো আলোচনা করা যেত; তাহলে দেবেশ রায়ের গল্পকার সত্তাটির বাঁকবদল ও উত্থানপতনকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা যেত। সে ভার অবশ্যই আগামীর সমালোচক তথা পাঠকরা তুলে নেবেন। জীবৎকালে কোনও লেখকের প্রতিভারই পরিপূর্ণ মূল্যায়ন হয়তো সম্ভব নয়। সময় যত পুরানো হয় একজন লেখক তথা শিল্পীকে আবিষ্কারের পরিধি ততই বিস্তৃত হয়। বিশ্বব্যাপী মহামারীর এই ক্রান্তিকালে ২০২০ এর ১৪ মে দেবেশ রায়ের এই প্রয়াণ নিঃসন্দেহে বড় বেদনার। প্রায় একই সময়ে বাংলার আকাশ থেকে ঝরে গেল দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ; দেবেশ রায় ও বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক, লেখক, চিন্তাবিদ ড. আনিসুজ্জামান। দুজনের প্রতিই আমার হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানিয়ে এই আলোচনার এখানেই ইতি টানলাম।
লেখক পরিচিতি : রাজু বিশ্বাসের জন্ম ১৯৮৯ -এ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বাজিতপুর গ্রামে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ। ১৫ বছর বয়সে প্রথম গল্প ‘টিয়া পাখির দ্বীপ’ প্রকাশিত হয় ‘সংবাদ প্রতিদিন’ পত্রিকায়। কবিতা দিয়েই লেখক জীবনের সূত্রপাত। ২০০৬ এ প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘প্রতীক্ষা শুধু ভালবাসার’ প্রকাশিত হয় কলকাতা বইমেলায়। ২০১৩-তে প্রকাশিত হয়েছে প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘ভাঙনকাল’ ও প্রবন্ধগ্রন্থ ‘অনন্ত মিছিলে অদীপ’। ২০১৬-তে প্রকাশিত হয় গল্পগ্রন্থ ‘এই সব শেয়ালেরা’। ২০১৭-তে ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত গল্প- ‘শবনগরী’। ‘শকুন্তলা এবং’ কাব্যগ্রন্থের জন্য ২০১৯-এ পেয়েছেন ‘মন শরৎ কবি সম্মান’।
আরও পড়তে পারেন….